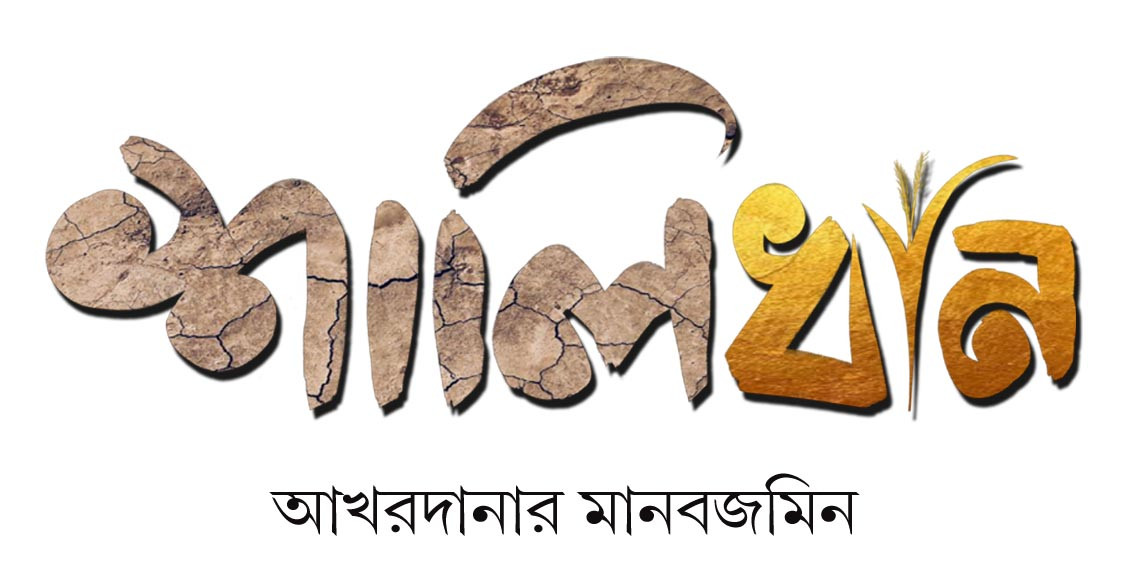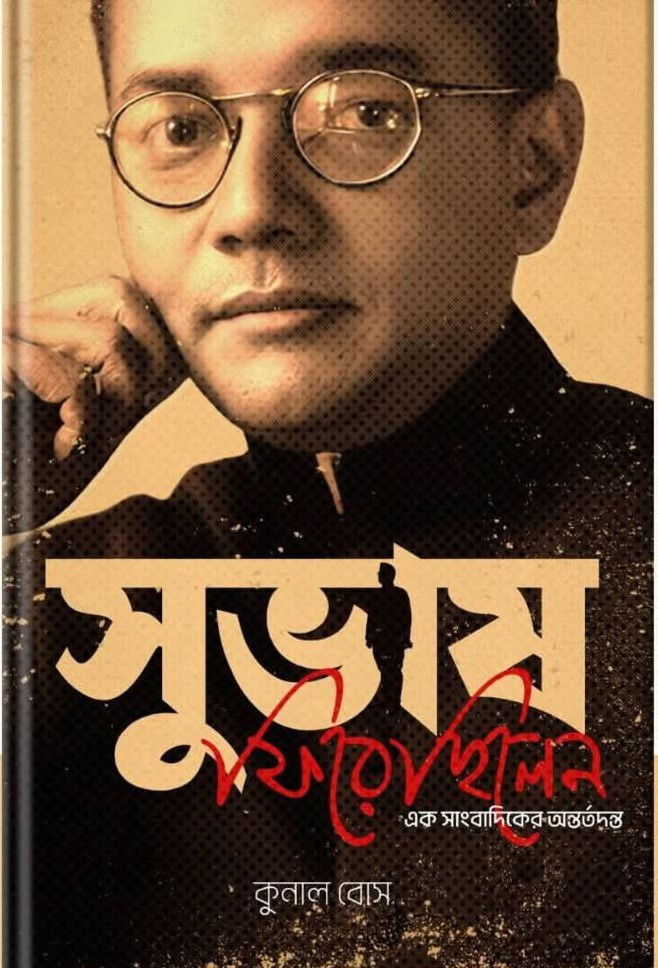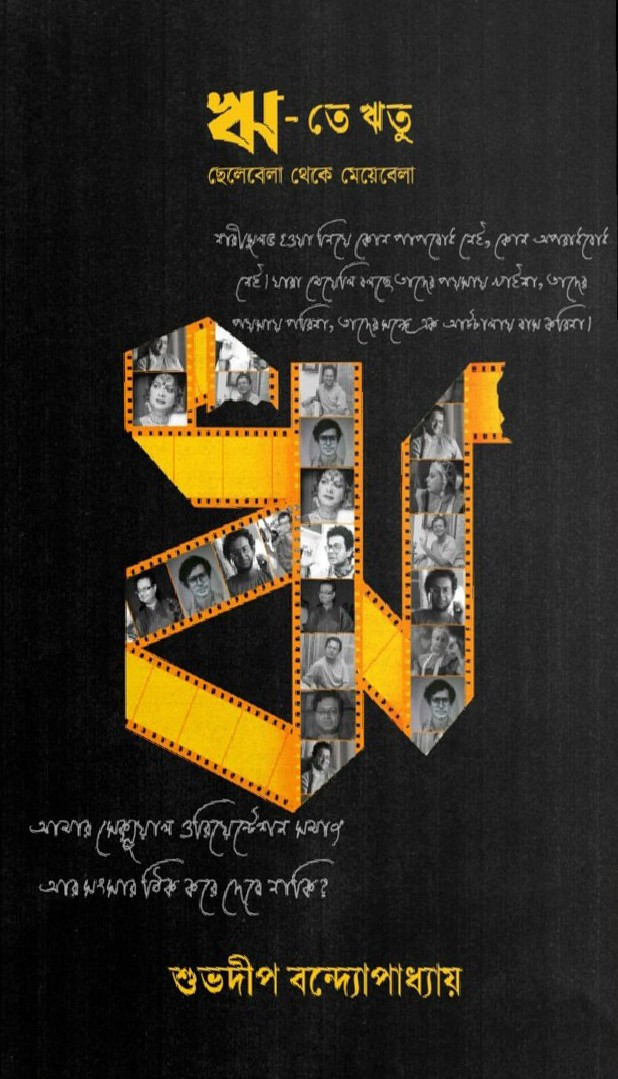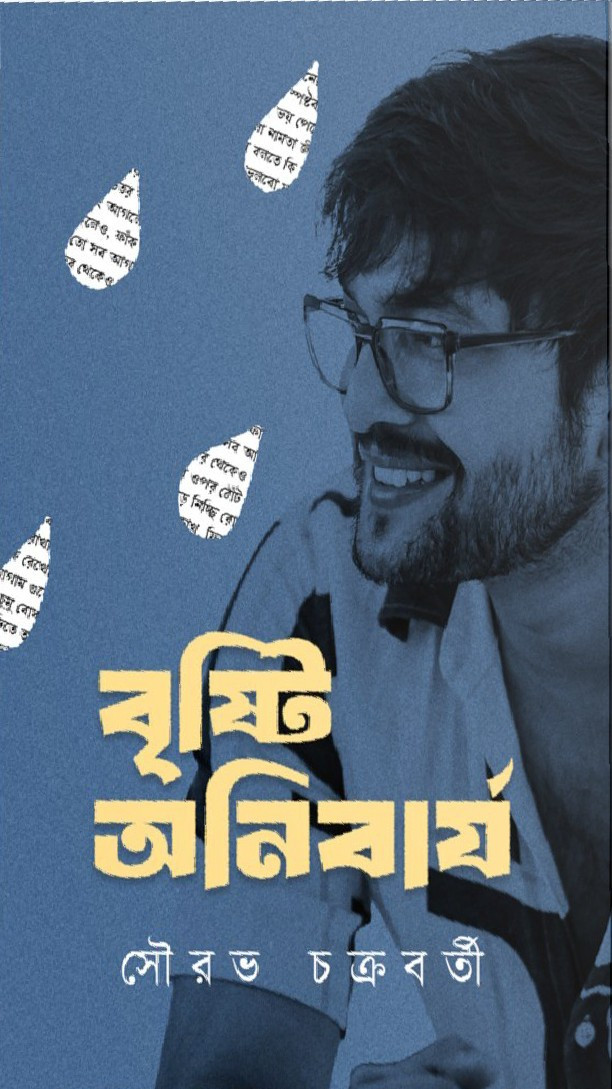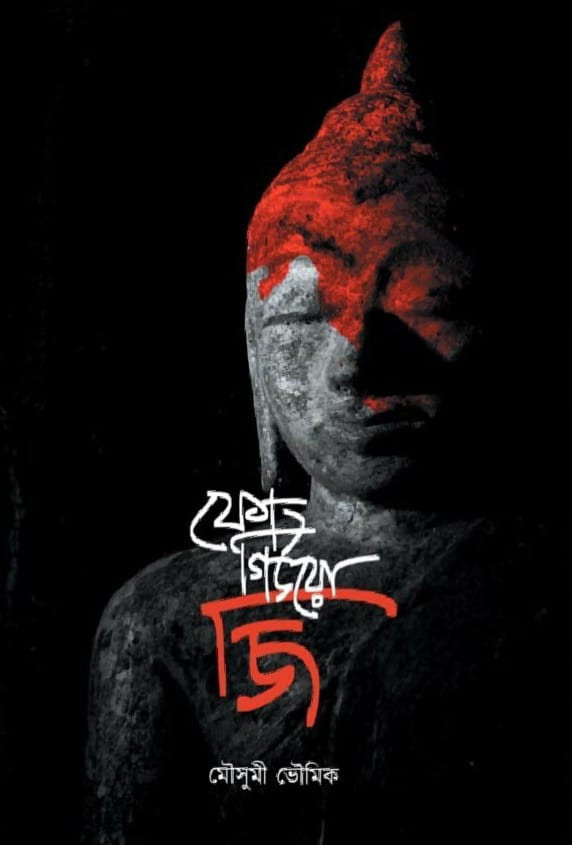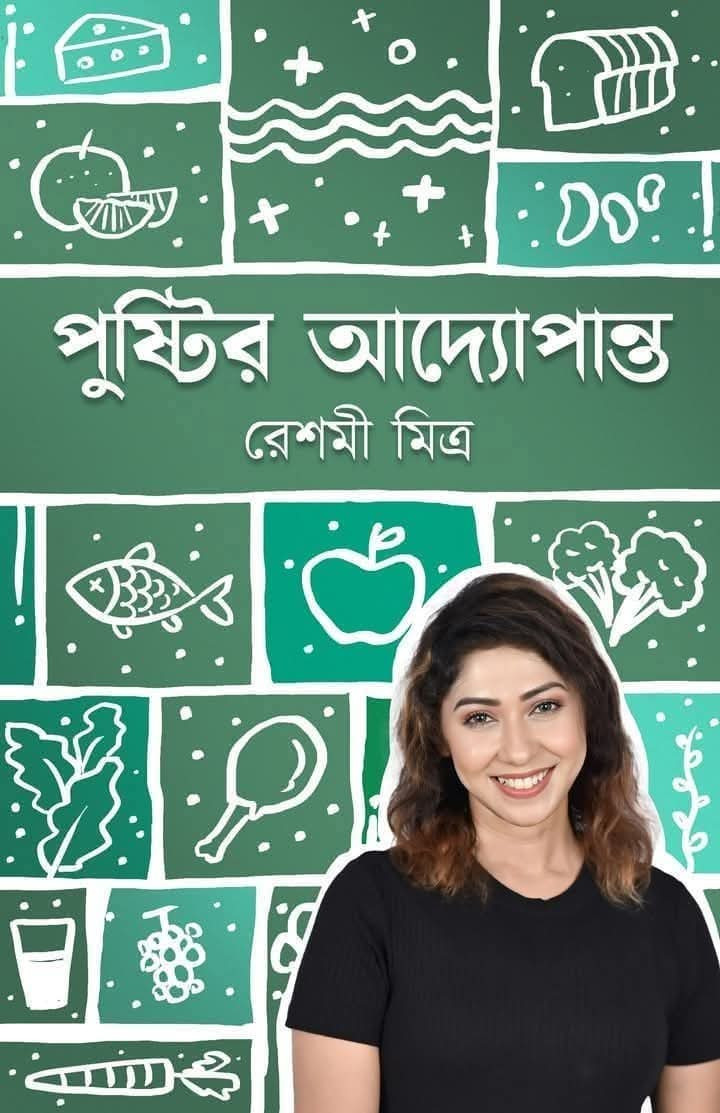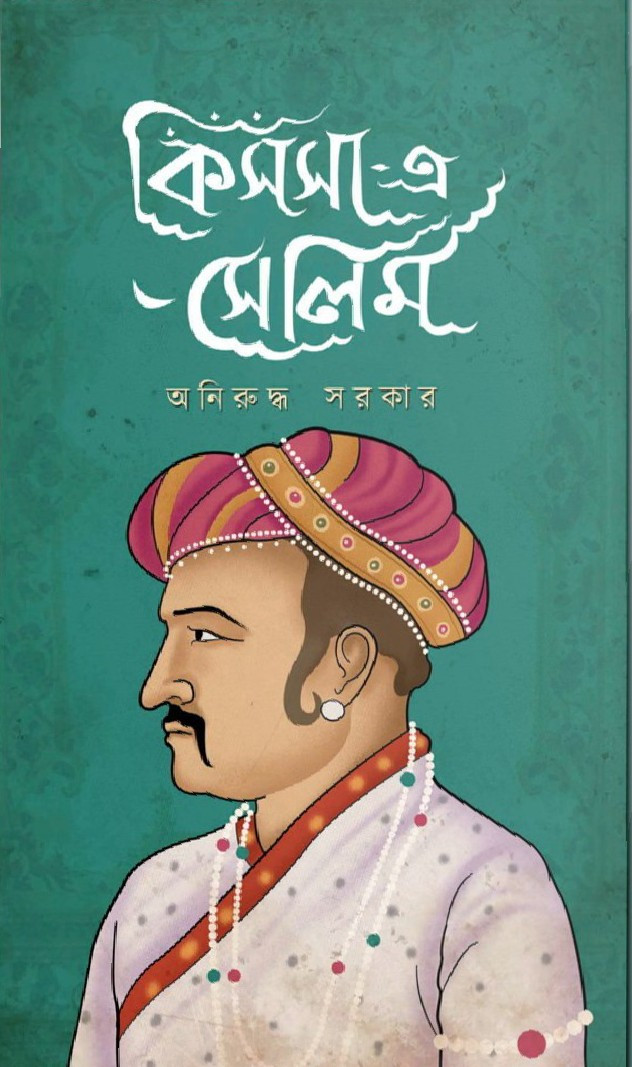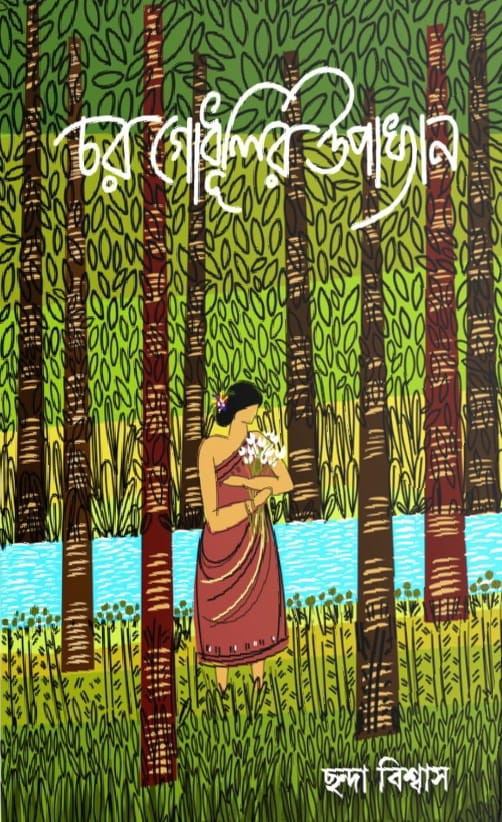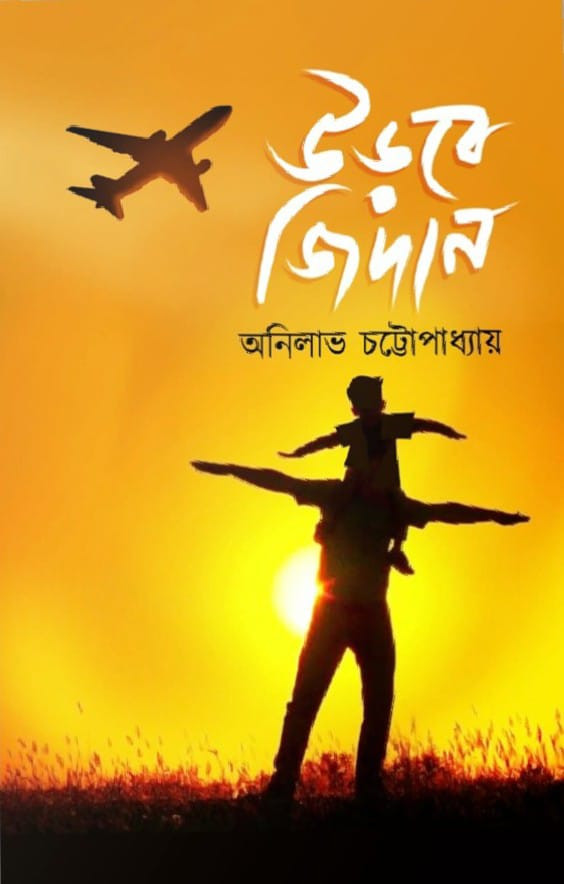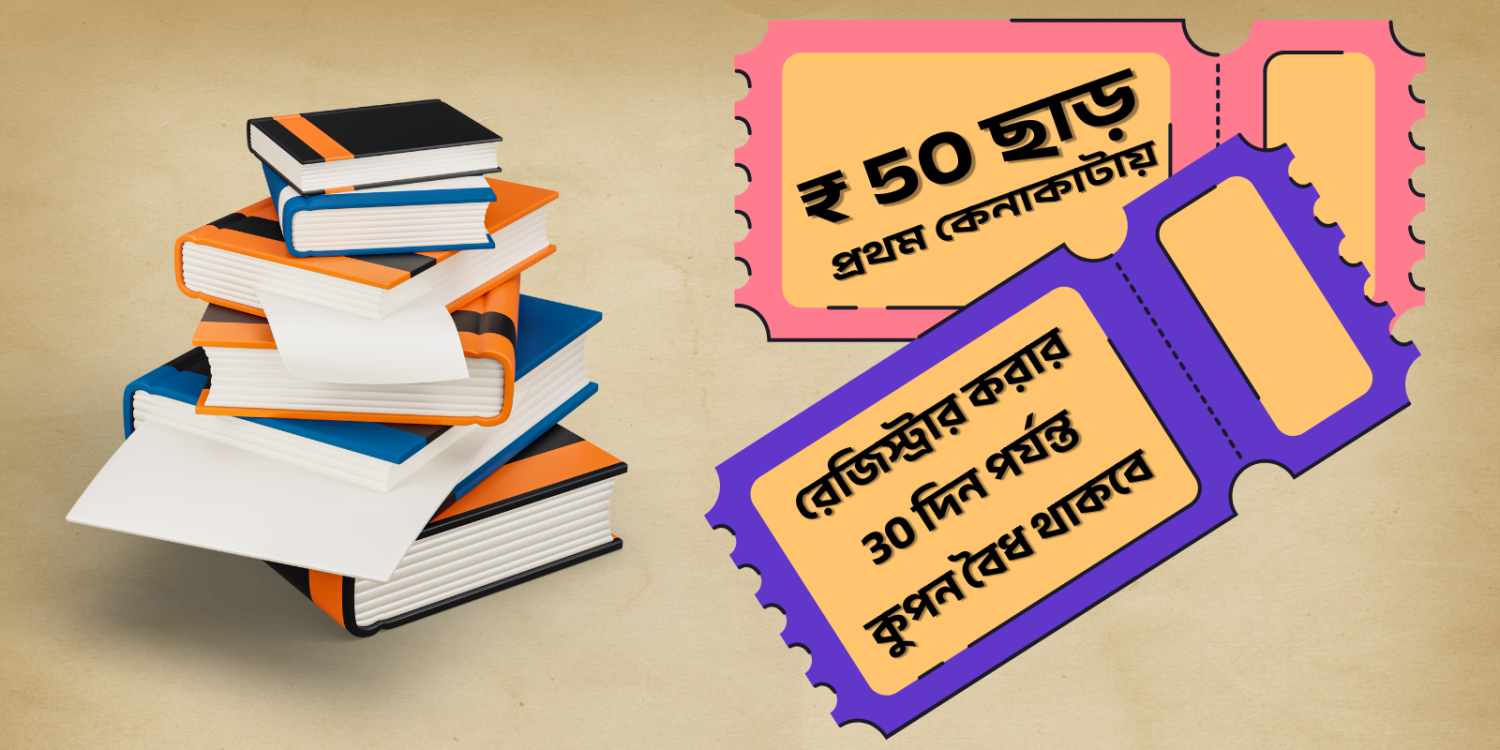বজ্রবিষাণ : কায়াসাধনার মায়াবাস্তব কাহিনি
উপন্যাস - বজ্রবিষাণ : কায়াসাধনার মায়াবাস্তব কাহিনি
লেখক - নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ - তন্ময় বিশ্বাস
লেখক নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস ‘বজ্রবিষাণ’ পাঠকের কাছে বিপুল সমাদর পেয়েছে। অনেক যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে গড়া এই উপন্যাসটির ব্যাপারে কিছু কথা বললে উপন্যাসে বর্ণিত সময়কাল বা যুগটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারে। উপন্যাসের মূল সুর যাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, সেই ভাবনা থেকেই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও বিন্যাস।
বৌদ্ধ ধর্মের রীতি-প্রকৃতির প্রতি লেখকের টান সুদীর্ঘ সময় ধরেই। সেই টান থেকেই এই উপন্যাস লেখার শুরু। থেরবাদ বা হীনযান থেকে প্রথম শতাব্দীতে মহাযান মতাদর্শের উদ্ভব দেখা যায়। আবার অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, এই মহাযান মতাদর্শ কীভাবে বজ্রযান সহজযান ও মন্ত্রযানের মধ্যে পথ খুঁজে নিল। যদিও এই বজ্রযান, সহজযান ও মন্ত্রযানের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য খুবই ক্ষীণ। তবু এই সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও সিদ্ধাচার্যরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতাদর্শগত তফাত সৃষ্টি করে কায়াসাধনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বর্ণিত শূন্যতাবাদের অনুসন্ধান করলেন। কেমন ছিল সেই কায়াসাধনার পথ?
এই কায়াসাধনার পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কোনো সিদ্ধাচার্যই দিয়ে যাননি। আবছা-ধূসর বর্ণনা হারিয়ে যায় চর্যাপদের কবিতাগুলির রহস্যময় ভাব ও ভাষায়। পদ রচনা, দোঁহা রচনা ও গ্রন্থ রচনার নিরিখে ঐতিহাসিক ভাবে চৌষট্টি জন সিদ্ধাচার্যের কথা জানা যায় কিন্তু এই চৌষট্টি জন সিদ্ধাচার্য ছাড়াও হয়তো আরো অনেক সিদ্ধাচার্য ও তাঁদের সাধনসঙ্গিনীরা ছিলেন, যাঁদের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। সেইরকমই কয়েকজন পরিচিত, অপরিচিত সিদ্ধাচার্যই এই উপন্যাসের চরিত্ররূপে উঠে এসেছেন। আলোচিত হয়েছে তাঁদের রহস্যময় তূরীয় জীবনচর্যার কথা।
অষ্টম শতাব্দীতে শ্রমণ অসংগ বৌদ্ধধর্মকে আর বেশি করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সুসভ্য নাগরিক ও গ্রামীণ জনসাধারণের পাশাপাশি আদিবাসী ও বনবাসী কৌম সমাজও এই সময় বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে আদিবাসী ও বনবাসী সমাজের লৌকিক পূজা-অর্চনা ও রীতি-নীতি বৌদ্ধধর্ম চর্চার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবক্ষয় শুরু হওয়ায় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তান্ত্রিকদের। ক্রমশ বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক রীতি, নীতি ও পূজা অর্চনার ধরণটি অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। দেহাশ্রয়ী হঠযোগ, নানা প্রকার বিভূতি ও সিদ্ধাই প্রদর্শন ও বিভূতির ব্যবহার সিদ্ধাচার্যদের দৈনন্দিনতার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।
অন্যদিকে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে জাদুবিদ্যার আঙ্গিক। ভারতে জাদুবিদ্যাচর্চা এক দীর্ঘ পরম্পরা। প্রথম শতাব্দীতে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাদুবিদ্যা বিভাগের খ্যাতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই বিভাগে অধ্যয়ন করতে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন বলে জানা যায়। এছাড়াও ভারতের পথে-প্রান্তরে দেখা মিলত নানা কলাকৌশল---- বিশেষত সম্মোহনী বিদ্যায় পারঙ্গম জাদুকরদের। তান্ত্রিক ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে এই জাদুবিদ্যা চর্চার দিকটিও প্রকাশিতব্য উপন্যাসে মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক।
এই উপন্যাসের আরেকটি দিক হল অপরসায়ন চর্চা। বিশ্বের নানা দেশে, বিশেষত মধ্য প্রাচ্য, মিশর ও ইউরোপে বহুল পরিমাণে হয়েছে এই অপরসায়ন চর্চা। ভারতের অপরসায়নবিদেরা এই ব্যাপারে পথিকৃত ছিলেন। প্রবাদপ্রতিম অপরসায়নবিদ নাগার্জুন ছিলেন দশম শতাব্দীর মানুষ। একাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে উপন্যাস রচিত হলেও দশম শতাব্দীর প্রভাবে এই যুগ প্রভাবিত। এই সময়ে বৌদ্ধ শ্রমণ নাগার্জুনের ছাত্রদল নির্জনে বসে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ নির্মাণ করে চলেছেন। অধ্যয়ন করছেন নানা অজানা বিষয়ে। এই ছাত্রদলের মধ্যেও বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
এই শতাব্দী যুদ্ধ-বিগ্রহেরও সময়। উত্তর ভারত সুলতান মামুদের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত। তবু সুলতান মামুদের সঙ্গে অন্ধকারে আলোক রেখার মতো আসেন জ্ঞান সাধক আল বিরুনি। সন্ধান করতে শুরু করেন ভারতাত্মাকে। শেষ পর্যন্ত খুঁজেও পান তাঁকে। ভারতবর্ষও তাঁকে বিমুখ করে না।
গল্প এগিয়ে চলে। মহারাজ প্রথম মহীপালদেবের সুশাসনে সুখী বঙ্গজন ও আরো কিছু মানুষ তাদের জীবন ও সমাজের রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। পাল বংশের রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত বঙ্গে একই সঙ্গে চলতে থাকে মহাযান ও বজ্রযানের প্রচার ও প্রসার। মহারাজ মহীপালদেব তিব্বত থেকে বৌদ্ধ সাধকদের আমন্ত্রণ করেন বঙ্গে। আয়োজিত হয় বৌদ্ধধর্মের আলোচনা চক্র। ক্রমাগত কাহিনি বঙ্গদেশের সীমানা পেরিয়ে গ্রীস পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
এই আশ্চর্য সময়ের প্রেক্ষিতে হাত ধরাধরি করে হাঁটে দুই তিনটি গল্প। মহারাজ প্রথম মহীপালদেব ও শ্রেষ্ঠী কন্যা লীলাবতীর প্রেমকাহিনি প্রথম গল্পের পটভূমি রচনা করে। দ্বিতীয় গল্পের নায়ক-নায়িকা হয়ে ওঠেন নামগোত্রহীন অতি সাধারণ দুই নর-নারী। তৃতীয় গল্পের মাঝে আসেন বজ্রযানী সাধক কঙ্কণপাদ ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী। এই তিনটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি রূপকথার মতো উপন্যাস।
রূপকথা, কারণ এ গল্পে ইচ্ছেপূরণ হয়, নর-নারীর কাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটে আর নটেগাছটি যথাসময়ে মুড়োয়।
পরিশেষে শুধু এটুকুই বলার যে, ইতিহাস সব কথা বলে না। প্রামাণ্য তথ্য যেহেতু সব সময় পাওয়া যায় না, সেহেতু গল্প সেখানে এগিয়ে চলে লেখকের কল্পনার একমাত্র যৌক্তিক সঙ্গী হয়ে। উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরে সেই ভাবনার সবটুকু উপস্থাপিত হয়েছে কিনা সে কথা বিচার করার ভার রইল পাঠকের উপরেই। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, এই উপন্যাস পাঠককে যেমন নিরাশ করেনি, তেমনই ইতিহাসভিত্তিক কল্পনাশ্রিত উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
-
₹470.00
₹499.00 -
₹199.00
-
₹250.00
-
₹150.00
-
₹372.00
₹399.00
সংশ্লিষ্ট বই
বই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা (0)
প্রবেশ করুন বা রেজিস্টার করুনআপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য
অন্যান্য প্রশ্নাবলী
কেউ এখনো কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি
-
₹470.00
₹499.00 -
₹199.00
-
₹250.00
-
₹150.00
-
₹372.00
₹399.00